ধর্মের নামে রাজনীতিই প্রমাণ করে আমরা মধ্যযুগীয়
ভারতবর্ষে এখনও যে ধর্মের নামে রাজনীতি হয় বা হচ্ছে, তাতেই প্রমাণ হয় আমরা আধুনিক নয়, চিন্তায়-চেতনায় এখনো মধ্যযুগে বাস করি।কারণ, আধুনিক যুগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে। কোন জাতি, নিজেকে আধুনিক বলে দাবি করতে চাইলে, এই বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। এর মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো হল ধর্ম-মুক্ত রাজনীতি। পৃথিবীর যেখানে যেখানে রাজনীতি ধর্মমুক্ত হয়েছে, সেখানে সেখানে রাজনৈতিক হিংসা হানাহানি অনেক কমে গেছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা, যা আধুনিকতার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।
মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায় ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি সম্পর্কিত থাকলে কি ভয়ংকর রাজনৈতিক সংকট তৈরি হয়। বোঝা যায়, কীভাবে নিরবিচ্ছিন্ন অস্থিরতা ও রাজনৈতিক হিংসা এবং প্রতিহিংসার দাপটে একটা জাতি শতধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। মূলত এ কারণেই, অসংখ্য ছোট ছোট, বলা ভালো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য। ফলে সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর নয়া সাম্রাজ্যবাদী নাগপাশ থেকে তারা কোনভাবেই বের হতে পারছে না।
এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো একই ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় মতাদর্শের দ্বারা সৃষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কারণে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে সদা সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। আর এই সংঘর্ষকে জিইয়ে রাখছে বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো। তারা নিজেদের দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্য নিয়ে ধর্মমুক্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থিতিশীল অবস্থা বজায় রেখেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য এরাই মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর ধর্মকেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছে।
আমাদের ভাবতে হবে, ধর্মকেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করতে গিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের মতো শতধাবিভক্ত হয়ে যাব না তো? আর এই পরিস্থিতি যদি সত্যিই তৈরি হয় তাহলে আমরা আবার নতুন করে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর ‘নয়া সাম্রাজ্যবাদী নীতি’র কবলে পড়ে যাব, যা আমাদের পরোক্ষ পরাধীনতার নাগপাশে আটকে ফেলবে। সুতরাং সাধু সময় থাকতে সাবধান হোন।
--------xx-------
পাঠকের মতামত, 👉 ফেসবুকে থেকে :
আমার উত্তর এখানে :
Shamim Ahmed কে :
প্রত্যেক যুগেরই কিছু ভালো, কিছু মন্দ দিক থাকে। ভালোটাকে সঙ্গে করে যুগান্তরের পথে হাঁটতে হয়। খারাপটাকে পিছনে রেখে আসতে হয়। সুতরাং কোন কোন ক্ষেত্রে মধ্যযুগে স্মরণীয় হয়ে আছে এবং থাকবে।
যখন কোন ফেলে আসা ধ্যান-ধারণাকে নতুন করে বিশেষ রাজনৈতিক স্বার্থে তুলে আনা হয়, তখন তা সমালোচনার অপেক্ষা রাখে। আমি সেটাই করেছি।
আমার মনে হয়, ভালোগুলোর কথা মাথায় রেখে খারাপগুলোকে এড়িয়ে চলা সঠিক নয়। আমার কথায়, সেই খারাপগুলোই উঠে এসেছে। ধর্মের নামে রাজনীতি প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় প্রথা। এটাই আসল সত্য। এইকথা ইউরোপীয় ঐতিহাসিক বললেন, না ভারতীয় ঐতিহাসিক বললেন, তার উপর গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে না। নির্ভর করে বিষয়ের মধ্যে থাকা সত্যের উপর।
আশা আমার কথা পরিষ্কার করতে পেরেছি। মনোযোগ দিয়ে লেখাটা পড়া এবং মতামত জানানোর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। ভালো থাকুন, সঙ্গে থাকুন। ভিন্ন মত থাকলে নিঃসংকোচে জানান।❤️❤️
Manirul Islam কে (১)
আপনার প্রশ্নের গভীরতা আমি বুঝি। বুঝি যুগের সীমাবদ্ধতার কথা। মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, কোন যুগ সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। অর্থাৎ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু প্রত্যেক যুগেরই কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা যুগান্তকারী। যুগান্তকারী বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করে এগিয়ে চলাই মানুষের কর্তব্য।
আমার ভাবনা কোন দেশ বা দেশের রাজনৈতিক সীমারেখায় আবদ্ধ নয়, কালের সীমারেখায় আবদ্ধ। সেই কাল বা সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে আমরা কিছু ধ্যান-ধারণাকে পিছনে ফেলে রেখে আসি, আর কিছু ধ্যান-ধারণাকে বহন করে যুগান্তরে পাড়ি জমাই। সেই ধ্যান-ধারণা যতদিন বিকল্পহীন থাকে, ততদিন তাকে আমরা মান্যতা দিই। যখন তার উন্নততর বিকল্প সামনে আসে, তখন তাকে ধরেই আবার নতুন করে পথ চলা শুরু করি। এটাই যুগের নিয়ম, এটাই ঐতিহাসিক সত্য।
ভারতীয় ইতিহাস সহ সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অনেক ভালো কিছুর সাথে আজকের সময়ের নিরিখে কিছু ধ্যান-ধারণা পিছিয়ে পড়া বলে বিবেচিত হয়। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ও ধর্মীয় ভাবাবেগ মিশিয়ে যুদ্ধের উন্মাদনা তৈরির মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের যে প্রথা তা প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয়। আধুনিক নয়। তাই আজকের যুগে তা যুগোপযোগী বলে মান্যতা পায় না।
সেটারই সমালোচনা রয়েছে আমার মন্তব্যের মধ্যে। আশা করি আমার ভাবনার বিশ্লেষণ করতে পেরেছি।
Manirul Islam কে (২)
আমি ধর্ম আর সাংস্কৃতিকে আলাদাভাবে দেখতেই স্বাচ্ছন্দ বোধ করি। কারণ একই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনুসারী হতে পারে। যেমন বাঙালির বা বাংলার যে সংস্কৃতি সেই সাংস্কৃতি বহন করে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মানুষ বেঁচে আছেন। অর্থাৎ সংস্কৃতির সঙ্গে ভাষার যে নৈকট্য, ধর্মের সঙ্গে ততটা নৈকট্য নেই।
কারণ হিসেবে কিছু বিষয় আমাকে এভাবে ভাবতে উৎসাহিত করে বা করছে। যেমন তর্কের খাতিরে যদি আপনার মতকে সমর্থন করি এবং ধর্মকে সংস্কৃতি বলেই মান্যতা দেই তবে কয়েকটি প্রশ্নের জন্ম হবে
১) ধর্ম যদি সংস্কৃতি হয়, তাহলে ইসলাম যেমন একদিকে ধর্ম অন্যদিকে সেটাই আরব জাতির সংস্কৃতি। তাহলে একই ইসলামিক সংস্কৃতির পরিচয়বাহী মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো কোন সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে এতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের জন্ম দিল?
২) সব লড়াই যদি সংস্কৃতির লড়াই হয়, তবে একই সাংস্কৃতির মানুষ পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করে কি করে?
আমার এ কারণেই মনে হয় যে, সংস্কৃতির নয়, মানব সভ্যতার ইতিহাসটা শ্রেণি সংগ্রামেরই ইতিহাস। শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রামের ইতিহাস। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের লড়াইয়ের ইতিহাস। এক্ষেত্রে সংস্কৃতি বা ধর্ম কখনো কখনো একটা অস্ত্র বা হাতিয়ার মাত্র। এবং জগৎ ও জীবনের প্রকৃত সত্যের সন্ধানে যারা খুবই দুর্বল অবস্থানে আছে, শাসক শ্রেণি এই হাতিয়ারের মাধ্যমে খুবই দ্রুত তাদের সমর্থন শক্তিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে ও অনুকূলে আনতে পারে।
৩) পৃথিবীর ইতিহাসে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের যে ইতিহাস আমরা পড়ি তা আপাতদৃষ্টিতে খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্ম বা সংস্কৃতির লড়াই মনে হতে পারে। কিন্তু আদতে সে লড়াই অর্থনৈতিক আধিপত্য লাভের লড়াই। অর্থনৈতিক আধিপত্য লাভের জন্য দরকার হয় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল। সেই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই করেছেন দুই পক্ষ। লড়াইয়ে জিততে গেলে দরকার মানুষের নিঃস্বার্থ সমর্থন এবং আত্মত্যাগ। ধর্ম নামক সংস্কৃতির নাম করে মানুষকে সহজেই এই লড়াইয়ে নামানো যায় বলেই একদিকে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী শাসকরা খ্রিস্টান ধর্মের দোহাই দিয়েছেন, অন্যদিকে মুসলিম প্রধান শাসকরা ইসলাম ধর্মের দোহাই দিয়েছেন।
প্রসঙ্গত বলে রাখি, ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির আলাদা কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে। ইসলামে মানবতাবাদ সহ অন্যান্য বেশ কিছু ইতিবাচক সমাজ দর্শন মানুষকে উৎসাহিত করেছে এই ধর্মের অনুসারী হতে। সে ইতিহাস আলাদা।
যদি ধর্ম (বা আপনার ভাষায় সংস্কৃতি) যদি লড়াইয়ের কারণ হত তবে সারা ইউরোপ জুড়ে একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যেত। আর তার নাম হতো খ্রিস্টান সাম্রাজ্য। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যে জন্ম নিত একটি অখন্ড ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা। কিন্তু তা কি হয়েছে? হয়নি। তার কারণ, সংস্কৃতি নয় লড়াইটা আসলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য লাভের লড়াই। আর সে কারণে এক ইসলামের আওতায় বহু রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে। একই ঘটনা ঘটেছে খ্রিস্টান ধর্মের ক্ষেত্রেও। এক ইউরোপ বহু জাতি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে গেছে।
বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় উত্তর আধুনিক শব্দ ব্যবহার হতেই পারে। এবং এই হওয়ার পিছনে কিছু তাত্ত্বিক ও বাস্তব ভিত্তি আছে। এখন বোঝার বিষয় হচ্ছে, ‘আধুনিক’ বলে যে সময়কে আমরা বোঝাচ্ছি এবং যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করছি তা কিন্তু সব রাষ্ট্রের মধ্যে নাও থাকতে পারে। যাদের মধ্যে থাকে তারাই কেবল আধুনিক। যে দেশের শাসকরা মৌখিক ভাবে গণতন্ত্রকে মানে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাকে বুড়ো আঙুল দেখায়, তারা আসলে গণতান্ত্রিক নয়। তাই আধুনিকও নয়। যেমন, বর্তমান ভারত সরকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় এসেছে, গণতন্ত্রের কথাই তারা বড়াই করে বলছে। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে তাদের কার্যকলাপ মোটেই গণতান্ত্রিক নয়। সুতরাং ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলেও গণতন্ত্র সেখানে খুবই নাজুক অবস্থায় রয়েছে। এ কারণেই আমি মধ্যযুগের প্রসঙ্গ এনেছি আমার facebook পোস্টে।
আধুনিক রাষ্ট্র দর্শনের বৈশিষ্ট্য অনুসারে দেখলে ইসরাইল আধুনিক রাষ্ট্র নয়। আধুনিক রাষ্ট্রে গনহত্যা চলে না। ধর্মীয় বিভাজনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চলে না। যারা তা করে, তারা নামেই আধুনিক, বাস্তবে নয়। সভ্য জগতের অভ্যন্তরে থাকলেও যেমন জানোয়ারা সভ্য নয়, তেমন আর কি!
ঠান্ডা লড়াইটাও সংস্কৃতির লড়াই নয়। এ লড়াইয়ের ভিত্তি প্রধানত দুটো। প্রাথমিক পর্বে এর ভিত্তি ছিল ধনতান্ত্রিক বনাম সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা কায়েম করার লড়াই। পরে এই লড়াই দুটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আধিপত্যবাদের লড়াইয়ে পরিণত হয়।
ইউরোপীয় নবজাগরণের সূত্র ধরে একসময় আধুনিকতার জন্ম হয় এবং দ্রুততার সঙ্গে তার প্রসার ঘটে। তারই সূত্র ধরে জাতি রাষ্ট্রের কনসেপ্ট দানা বাঁধে। এই জাতিরাষ্ট্রের ধারণাই ইউরোপ ও এশিহাসহ পৃথিবীর মানচিত্র আমূল পাল্টে দেয়। মনে রাখতে হবে, এই জাতি রাষ্ট্রের ধারণাও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। ধর্ম নামক সংস্কৃতির মাধ্যমে নয়। তুরস্ক রাষ্ট্রের ভাঙ্গন, ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন - সবই এই নতুন রাষ্ট্র দর্শনের কল্যাণের সংঘটিত হয়।
কমিউনিজমকে আপনি সংস্কৃতি বলে ভাবতেই পারেন। যদি ভাবেন, একই রকম ভাবে উল্টোদিকে থাকা ক্যাপিটালিজমও সংস্কৃতি হিসেবে আপনার সামনে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হলো, কমিউনিজম ধর্ম দর্শনকে উপেক্ষা করে ধন বৈষম্যকে হাতিয়ার করে তার প্রচার ও প্রসার ঘটে। অন্যদিকে ক্যাপিটালিজম ধনো বৈষম্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তার প্রচার প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করে। কোন কোন দেশ এক্ষেত্রে ধর্ম দর্শনকে উপেক্ষা করে যেমন আমেরিকা। আবার কেউ কেউ ধর্ম দর্শনকেই হাতিয়ার করে। বর্তমান ভারতের সরকার সেটাই করার চেষ্টা করছে। সুতরাং এ দুইয়ের মধ্যে ধর্ম বিষয়টি মোটেই সামনাসামনি দাঁড়িয়ে যুদ্ধং দেহি মূর্তিতে দাঁড়িয়ে নেই। আছে অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারকে সামনে রেখে লড়াইয়ের ময়দানে। যুদ্ধং দেহি মূর্তিতে।
Emanul Haque কে
শ্রদ্ধেয় সাথি, এরকম অন্ধ সংকীর্ণতা ছিল না - কথাটা আমিও মানি। কারণ, ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসটা আমি পড়েছি এবং ইতিহাস আমার পড়ানোর বিষয়ও বটে, তাই আমি জানি। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক ছিল না, এটা বলা বোধ হয় যাবে না। কারণ হিসেবে অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। তার মধ্যে যেটা আমাকে বিশেষভাবে ভাবায়, তা হল আকবরের দ্বীন-ই-ইলাহী নামে একটি সমন্বয়বাদী ধর্মমত প্রবর্তনের চেষ্টা করার বিষয়টা। ধর্ম আর রাজনীতি যদি পরস্পর হাত ধরাধরি করে না চলতো তবে আকবরের এই সমন্বয়বাদী ধর্মচিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হল কেন?
আর হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন, ইউরোপিয়ান মধ্যযুগ আর আমাদের দেশের মধ্যযুগ এক নয়। আমাদের মধ্যযুগ, আমার মতে, এখনো কাটেনি। ইউরোপীয় মধ্যযুগ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। সেটা মাথায় রেখেই তো পোস্টটা করলাম। তা না হলে তো এই পোস্টের কোন অর্থই হয় না।
আপনি মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন এবং মতামত দিয়েছেন। এজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করি আমার ভাবনা পরিষ্কার করতে পেরেছি।
Asoke Chakravarty কে
পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ধর্মের নামে রাজনীতি চলছে এ কথা ঠিক। কিন্তু সব জায়গায় চলছে এবং সমান মাত্রায় চলছে এ কথা ঠিক নয়। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে ধর্মকে এভাবে নগ্ন ভাবে রাজনীতির ময়দানে নামানো হয় না। সেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলা হয়, মান্যতা দেয়ার বিষয়টি ইসু হয়। কিন্তু ধর্মান্ধতার জিগির তুলে একটি নির্দিষ্ট সাম্প্রদায়কে টার্গেট করে রাজনীতি করা হয় না। আমাদের দেশের সঙ্গে একমাত্র ইসরাইলকেই তুলনা করা যায়।
আবার অনেক দেশ আছে যেখানে রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে কোনভাবেই একাশনে বসতে দেয়া হয় না। ধর্ম কখনোই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পায় না। পৃথিবীর ইতিহাসে এই সমস্ত দেশ সমীহ করার মত জায়গায় পৌঁছে গেছে। আর এ কথাগুলো ভুললে, সত্যের অপলাপ শুধু নয়, অন্ধত্বকে স্বীকৃতি দেয়া হয়।
সুতরাং ধর্মান্ধতা এবং তাকে রাজনীতিক স্বার্থে ব্যবহার করাটা সার্বজনীন যেমন নয়, তেমন চিরন্তনও নয়। কারণ একসময় পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র গুরুরাই ধর্মগুরু ছিলেন। বর্তমান সময়ে সেটা যথেষ্ট পরিমাণে কমে গেছে। মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশকে বাদ দিয়ে বাকি পৃথিবীর দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটা একান্তই আমার মতামত ও বিশ্লেষণ।
আমার মতামত আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং আপনার মতামত সরাসরি সামনে এনেছেন জেনে খুশি হলাম।
খুব ভালো থাকুন এবং আনন্দে থাকুন। সময় পেলে অবশ্যই সঙ্গে থাকুন এবং আপনার মতামত নির্দ্বিধায় আমার সামনে রাখুন।
আবার অনেক দেশ আছে যেখানে রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে কোনভাবেই একাশনে বসতে দেয়া হয় না। ধর্ম কখনোই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পায় না। পৃথিবীর ইতিহাসে এই সমস্ত দেশ সমীহ করার মত জায়গায় পৌঁছে গেছে। আর এ কথাগুলো ভুললে, সত্যের অপলাপ শুধু নয়, অন্ধত্বকে স্বীকৃতি দেয়া হয়।
সুতরাং ধর্মান্ধতা এবং তাকে রাজনীতিক স্বার্থে ব্যবহার করাটা সার্বজনীন যেমন নয়, তেমন চিরন্তনও নয়। কারণ একসময় পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র গুরুরাই ধর্মগুরু ছিলেন। বর্তমান সময়ে সেটা যথেষ্ট পরিমাণে কমে গেছে। মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশকে বাদ দিয়ে বাকি পৃথিবীর দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটা একান্তই আমার মতামত ও বিশ্লেষণ।
আমার মতামত আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং আপনার মতামত সরাসরি সামনে এনেছেন জেনে খুশি হলাম।
খুব ভালো থাকুন এবং আনন্দে থাকুন। সময় পেলে অবশ্যই সঙ্গে থাকুন এবং আপনার মতামত নির্দ্বিধায় আমার সামনে রাখুন।
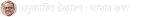
প্রাচীন যুগ কেনো বলছেন না.......???
উত্তরমুছুনমধ্যযুগ কেনো বলছেন..........???
বলছি না মানে এই নয় যে, সেখানে এই পরিস্থিতি ছিল না। অবশ্যই ছিল এবং অনেক বেশীই ছিল। কিন্তু আমি এখানে তা বলিনি।
মুছুনবলিনি, তার কারণ হল, তা বলার প্রয়োজন হয় না। মধ্যযুগ আর আধুনিক যুগ পিঠোপিঠি। তাই পরস্পর পরস্পরের মধ্যে অনেকটাই থেকে যায় বহুদিন ধরে। তারপর আস্তে আস্তে তারা বিচ্ছিন্ন হয়।
আমরা এখনও সেই বিচ্ছিন্নতার কাজটা করে উঠতে পারিনি। প্রাচীন যুগ তো অনেক অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছি। তার সঙ্গে তুলনার প্রয়োজন তাই অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে আমার কাছে।
তাই তা বলার প্রয়োজন বলে মনে হয়নি। এই আর কী!