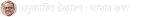ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি দরদ না ভন্ডামি! ধর্মের ভিত্তিতে সংখ্যালঘু —এই বিষয়টিকে আপনি যদি স্বীকৃতি দেন (এভাবে ভাবা যদিও অযৌক্তিক) এবং নিজের ধর্মের মানুষ হিসেবে আপনি যদি কোন জনগোষ্ঠীকে আপন বলে ভাবেন, তাদের দুঃখ-কষ্ট যদি আপনাকে কষ্ট দেয়, তাহলে নিজের দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি আপনার সবচেয়ে বেশি নজর রাখা উচিৎ। কারণ, আপনার দেশে যারা সংখ্যালঘু, অন্য কোন দেশে তারাই সংখ্যাগুরু। আপনার দেশে সংখ্যালঘুরা যদি শান্তিতে থাকতে না পারেন, বৈষম্যের শিকার হওয়াকে আপনি যদি আটকাতে না পারেন, তাহলে অন্য দেশে আপনার ধর্মের সংখ্যালঘু মানুষকে নিরাপদ রাখার বিষয়টি অযৌক্তিক এবং কার্যত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। মনে রাখতে হবে, ধর্মীয় কারণে যারা সংখ্যালঘুদের বঞ্চিত করেন, তারা মানবিক গুণসম্পন্ন নয়। তারা সম্পূর্ণ স্বার্থান্ধ এক শ্রেণি, যারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পদের সুষম বন্টন তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। অন্যদিকে সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থায় তারা বর্ণবাদে (উঁচুজাত ও নিচুজাত তত্ত্বে) বিশ্বাসী। আপনি যদি আপনার দেশে এই স্বার্থান্ধ ও ধর্মান্ধ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হন, তবে আপনার মাথায় রাখা উচিত, যে আপনার মতো এই শ্রেণির মানব...
ধর্মের নামে রাজনীতিই প্রমাণ করে আমরা মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে এখনও যে ধর্মের নামে রাজনীতি হয় বা হচ্ছে, তাতেই প্রমাণ হয় আমরা আধুনিক নয়, চিন্তায়-চেতনায় এখনো মধ্যযুগে বাস করি। কারণ, আধুনিক যুগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে। কোন জাতি, নিজেকে আধুনিক বলে দাবি করতে চাইলে, এই বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। এর মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো হল ধর্ম-মুক্ত রাজনীতি। পৃথিবীর যেখানে যেখানে রাজনীতি ধর্মমুক্ত হয়েছে, সেখানে সেখানে রাজনৈতিক হিংসা হানাহানি অনেক কমে গেছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা, যা আধুনিকতার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায় ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি সম্পর্কিত থাকলে কি ভয়ংকর রাজনৈতিক সংকট তৈরি হয়। বোঝা যায়, কীভাবে নিরবিচ্ছিন্ন অস্থিরতা ও রাজনৈতিক হিংসা এবং প্রতিহিংসার দাপটে একটা জাতি শতধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। মূলত এ কারণেই, অসংখ্য ছোট ছোট, বলা ভালো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য। ফলে সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর নয়া সাম্রাজ্যবাদী নাগপাশ ...