স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা, আত্মপরিচয়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক
প্রত্যেক শিক্ষিত বাবা-মা চায়, তার সন্তান তার নিজস্ব আইডেন্টিটি (পরিচয়) গড়ে তুলুক। বাবা-মায়ের পরিচয়ের বাইরেও তার নিজস্ব পরিচয় গড়ে উঠুক। বাবা মায়ের পরিচয় হল একটি জৈবিক পরিচয়, যা জন্ম সূত্রে পাওয়া। পারিবারিক সম্পর্কের আলিঙ্গনে বাধা এক অদৃশ্য কিন্তু অটুট ও শক্তিশালী বন্ধন। এই বন্ধনকে ছিঁড়ে ফেলার সঙ্গে আত্মপরিচয়ের কোন নিকট সম্পর্ক নেই। বা বলা ভালো, জন্মসূত্রে পাওয়া পারিবারিক সম্পর্কের বন্ধন, যার সঙ্গে নিজস্ব পরিচয় গড়ে তোলার কোন বৈপরীত্যের সম্পর্ক নেই। কেননা, এই সম্পর্ক ছিড়ে ফেললে আত্মপরিচয় গড়ে তোলার ভীত দুর্বল হয়ে পড়ে। কারণ, এই ভিত গড়ে তুলতে, এই সম্পর্কের সাপোর্ট খুবই জরুরী। এই সাপোর্ট ছাড়া ধণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আত্মপরিচয়ের ভীত এবং তার উপরে ইমারত গড়ে তোলার পরিকল্পনা দিবাস্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়।এই পরিচয় তখনই গড়ে ওঠে, যখন তার নিজস্ব আর্থিক শক্তি তৈরি হয়। এই শক্তি অর্জনের মূল হল ইচ্ছা শক্তি। এই ইচ্ছা শক্তি তখনই তার মধ্যে বাড়তে থাকে, যখন সে বোঝে, বাবা-মায়ের সম্পদ আসলে তার সম্পদ নয়। পরবর্তী সংসার জীবনে স্বামী বা স্ত্রীর সম্পদও আসলে তার নয়। এই ভাবনা মানুষকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার দিকে প্ররোচিত করে। এই ভাবনাকে যদি স্বাগত জানায় তবে তার আত্মপরিচয় গড়ে ওঠে। তৈরি হয় নিজস্ব আইডেন্টিটি।
সন্তান যদি এই দাবি করে, সম্পর্কের খাতিরে তার পিতা মাতার সম্পদের উপর তার নিজস্ব দাবি আছে, তাহলে তাকে এও স্বীকার করে নিতে হবে যে, সে আত্মনির্ভরশীল নয়। সুতরাং তার আত্মপরিচয়ও কোনদিন তৈরি হবে না।
ছেলেদের ক্ষেত্রে আত্মপরিচয়ের এই সংকট একসময় দূর হয়ে যায়। যদিও সেই পরিচয়, খুব বেশি আত্মসম্মান এবং মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ হিসাবে বাঁচতে সাহায্য করে না। আর্থিক দৈন্য, সামাজিক সম্পর্কে সীমাবদ্ধতা নিয়ে তাকে হীনমন্যতায় ভুগতে হয়। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে এই সংকট ভয়ানক আকার ধারণ করে। মেয়েকে প্রথমে পিতা মাতার পরিচয় নিয়ে বাঁচতে হয়। মধ্য বয়সে স্বামীর পরিচয় বাঁচতে হয়। এবং শেষ বয়সে সন্তানের পরিচয় নিয়ে তাকে এই পৃথিবী ছাড়তে হয়। নিজস্ব ঘর, নিজস্ব সংসার, সর্বোপরি নিজের পরিচয়হীনতার কলঙ্ক নিয়েই তাকে বিদায় নিতে হয়। জীবনভর অক্লান্ত পরিশ্রমের পরেও গড়ে ওঠে না তার নিজস্ব আইডেন্টিটি।
মেয়েদের ক্ষেত্রে আমাদের সমাজে রয়েছে নানা সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা। পুরুষ মানুষের উপর নির্ভরশীলতা, ধর্মীয় বিধান তাকে বাধ্য করে এই প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে। ছোটবেলা থেকে শেখানো হয়, এগুলো প্রতিবন্ধকতা নয় বরং প্রতিবিধান যা ঈশ্বর প্রদত্ত। এই শেখানোর মধ্য দিয়েই স্বাধীনতা হীনতাকেই সে স্বাধীনতা বলে বুঝতে এবং মানতে শেখে। এভাবেই চলছে আমাদের দেশের সমাজ সংসার। বংশ-পরম্পরায় অধিকাংশ মানুষই এই ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছেন।
এই পরিস্থিতিতে যদি কোন মেয়েকে তার আত্মপরিচয় নিয়ে ভাবতে হয়, তবে প্রথম পদক্ষেপে নিতে হয় তার পিতামাতাকে। কোন পিতা-মাতা সেটা পারবেন? তারাই পারবেন, যারা আধুনিক মানুষ। কারণ, নারীর আত্মপরিচয়ের যে দর্শন তার আঁতুড় ঘর হল আধুনিকতা। আধুনিকতার ভিত্তি ভূমি তৈরি হয় আরও কিছু প্রগতিশীল চেতনার সমন্বয়ে। যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবতাবাদ হল সেই প্রগতিশীল চেতনাগুলোর অন্যতম প্রধান অঙ্গ। এই সমস্ত মহামূল্যবান প্রগতিশীল চেতনার অধিকারী হওয়া ছাড়া কোন পিতা-মাতার পক্ষে তার কন্যা সন্তানের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখা সম্ভব নয়। তাই একমাত্র আধুনিক ও প্রগতিশীল চিন্তা চেতনার অধিকারী বাবা-মার পক্ষেই সম্ভব সন্তানকে আত্মনির্ভর হয়ে গড়ে ওঠার সাপোর্টিং রসদ।
আরও পড়ুন : আধুনিকতা কী, কেন এবং কীভাবে তা অর্জন করা যায়?
এখন প্রশ্ন হল, বাবা মা চাইলেই কি এটা সম্ভব? না। বাবা-মায়ের চাওয়াটা যেমন প্রাথমিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত, ঠিক তেমনি মেয়ে সন্তানকেও তা আন্তরিকভাবে চাইতে হবে। তাহলে প্রশ্ন হল কোন সন্তান এই চাওয়ার সাহস দেখাবে? যার মধ্যে প্রশ্ন করার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। আসার কথা হল, এই প্রশ্ন করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায় একজন মানব শিশু। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। কিন্তু জানানোর পরপরই সমাজ এবং পরিবার তাকে প্রশ্ন না করতে শেখায়। একসময় সে প্রশ্ন করতেই ভুলে যায়। প্রশ্ন করাকে ‘পাপ’ বলে ভাবতে শেখে। কে শেখায়? এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শিক্ষাগুরু হচ্ছেন তার পিতামাতা। তারপর তার পরিবারের অন্য প্রবীণ মানুষেরা। এবং সবশেষে তার সমাজ, যে সমাজে সে একটু একটু করে বেড়ে উঠছে।
এখানেই বাবা-মায়ের সবচেয়ে বড় ভূমিকা। ছোট থেকেই সন্তানকে প্রশ্ন করতে শেখাতে হবে। প্রশ্ন করতে সে তখনই শিখবে, যখন তাকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে প্রশ্ন করার।
কিন্তু এই স্বাধীনতার মানে এই নয় যে, অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত মানুষের (নিজের বাবা-মা সহ) পরামর্শকে সে অস্বীকার করবে, স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের অজুহাতে। এটা করলে সে নিজেকে স্বেচ্ছাচারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলবে। স্বাধীনতার সঙ্গে স্বেচ্ছাচারের কোন নিকট কিংবা দূরবর্তী সম্পর্ক নেই, যার কারণে স্বাধীনতা খর্ব হয়। বরং এদের মধ্যে রয়েছে সতত বৈপরীত্যের একটি কঠিন সম্পর্ক। পারস্পরিক মত বিনিময় এবং যুক্তি, তথ্য ও বুদ্ধি দ্বারা জারিত সিদ্ধান্তের প্রতি মান্যতা হল স্বাধীনতার মূল চাবিকাঠি। এটাকে অস্বীকার করাটা স্বেচ্ছাচারিতা।
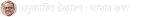
মন্তব্যসমূহ
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন